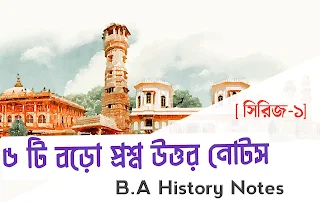- : সূচিপত্র :-1. মুঘল সম্রাট আকবরের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বিবরণ দাও?
2. মুঘলসাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি আলােচনা কর?
3. মধ্যযুগের ভারতবর্ষের বা মুঘল যুগের ইতিহাসের প্রধান উপাদানগুলি সম্বন্ধে আলােচনা কর?
4. আকবরের রাজপুতনীতিটি পর্যালােচনা কর বা এই নীতির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল?
5. মুঘল সম্রাটের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত লেখো?--------------------------------------------------------------------❋ 1. মুঘল সম্রাট আকবরের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বিবরণ দাও?What is the Land Revenue System of Akbar?
2. মুঘলসাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি আলােচনা কর?
3. মধ্যযুগের ভারতবর্ষের বা মুঘল যুগের ইতিহাসের প্রধান উপাদানগুলি সম্বন্ধে আলােচনা কর?
4. আকবরের রাজপুতনীতিটি পর্যালােচনা কর বা এই নীতির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল?
5. মুঘল সম্রাটের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত লেখো?
ロ ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ কৃষি হলো অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বর্তমান যুগ থেকে আকবরের সময় পর্যন্ত দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করত। তাই আকবরের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা আলোচনা করতে হলে আমাদের তৎকালীন গ্রামের অর্থনীতি কে আলোচনা করতে হবে, ফলে মুসলমান শাসকদের মধ্যে আলাউদ্দিন খলজী প্রথম জমি জরিপ করে গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং একটা নির্দিষ্ট রাজস্ব ব্যবস্থার সূচনা করে । আলাউদ্দিনের পর শেরশাহ প্রথম এই ব্যবস্থা উপলব্ধি করেন, ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে ভূমি রাজস্ব হলো শাসন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক মানদন্ড। শেরশাহের রাজত্বকালে অল্প কয়েক বছর হওয়ায় তাঁর রাজস্ব ব্যবস্থা সর্বোপরি কার্যকর হয়ে ওঠেনি বরং পরবর্তীকালে আকবর মূলত শেরশাহ কর্তৃক অনুসৃত নীতি অনুযায়ী রাজস্ব পদ্ধতিকে আরো বিজ্ঞানসম্মত করে আধুনিক রাজস্ব ব্যবস্থার সূচনা করেন।
আকবরের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ; মূল উদ্দেশ্য ছিল জনকল্যাণমূলক। আকবর তার সম্রাজ্য রাজস্ব পদ্ধতি পুনর্গঠন এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তার রাজত্বকাল এর প্রথম দিকে খাজা আব্দুল মজিদ , মোজাফর তরবতী , ও টোডরমলের সাহায্যে রাজস্ব্ পদ্ধতি সংস্কারের চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য তরবতী 10 জন কানুনগোকে নিযুক্ত করেন। কানুনগো রা সুনিশ্চিত কতগুলি সুপারিশ করে কিন্তু উজবেক দের বিদ্রোহের জন্য তাদের পরিকল্পনা কার্যকর হয় উঠেনি। 1575 খ্রিস্টাব্দে জায়গীর গুলি উচ্ছেদ করা হয় এর পরিবর্তে সমগ্র সাম্রাজ্যকে 182 পরগনায় বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক পরগনায় একজন করে করোরী রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু করোরীদের অত্যাচারও উৎকোচ গ্রহনের ফলে কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে ফলে আকবর করোরীদের অফিস বন্ধ করে দেন এবং পুরনো রাজস্ব পদ্ধতি চালু করে।
এরপর 1573 খ্রিস্টাব্দে গুজরাট বিজয়ের পর টোডরমল গুজরাটের সমস্ত জমি জরিপ করে ভূমির গুণ ও আয়তন অনুসারে রাজস্ব স্থির করেন। 1575 খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ-বিহার ছাড়াও সাম্রাজ্যের সকল জমি খলিসা বা খাস জমিতে পরিণত করা হয়। এরপর 1582 খ্রিস্টাব্দে টোডরমল দেওয়ানী আশরাফৎ অথবা প্রধান রাজস্ব সচিব এ নিযুক্ত হন । টোডরমল গজ-ই-ইলাহি এক বিঘার আয়তন এক এককের 0.59 ভাগের সমান মাপের সমগ্র সাম্রাজ্যের জমিজরিপ যেমন এক বছরের জন্য রাজস্ব পরিমাণ ধার্য করা হয় এটি একসালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত আর পরবর্তীকালে আকবর 10 বছরের ফসলের নিরিক্ষে রাজস্ব নির্দেশ দিলে সেটি দশসালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত হয় । ফলে ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব এই ব্যবস্থাকে চরম দাওয়াই বলে অভিহিত করেছেন।1582 খ্রিস্টাব্দে টোডরমল রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করেন এবং তিন প্রকার রাজস্ব ব্যবস্থার প্রচলন করেন। তাঁর রাজস্ব নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রথমতঃ আবাদি জমি জরিপ দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকবিহার উৎপন্ন শষ্যর নিয়ন্ত্রণ তৃতীয়তঃ প্রত্যেক বিঘার রাজস্ব হার নির্ধারণ করা । এন.এ. সিদ্দিক জানিয়েছেন আকবরের সময় রাজস্ব নির্ধারণের প্রথা হিসেবে ছিল (ক) জাবতি প্রথা (খ) নাসাক (গ) গাল্লাবকস্ এবং কয়েকটি অতি প্রচলিত প্রথা ।
আকবরের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ; মূল উদ্দেশ্য ছিল জনকল্যাণমূলক। আকবর তার সম্রাজ্য রাজস্ব পদ্ধতি পুনর্গঠন এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তার রাজত্বকাল এর প্রথম দিকে খাজা আব্দুল মজিদ , মোজাফর তরবতী , ও টোডরমলের সাহায্যে রাজস্ব্ পদ্ধতি সংস্কারের চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য তরবতী 10 জন কানুনগোকে নিযুক্ত করেন। কানুনগো রা সুনিশ্চিত কতগুলি সুপারিশ করে কিন্তু উজবেক দের বিদ্রোহের জন্য তাদের পরিকল্পনা কার্যকর হয় উঠেনি। 1575 খ্রিস্টাব্দে জায়গীর গুলি উচ্ছেদ করা হয় এর পরিবর্তে সমগ্র সাম্রাজ্যকে 182 পরগনায় বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক পরগনায় একজন করে করোরী রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু করোরীদের অত্যাচারও উৎকোচ গ্রহনের ফলে কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে ফলে আকবর করোরীদের অফিস বন্ধ করে দেন এবং পুরনো রাজস্ব পদ্ধতি চালু করে।
এরপর 1573 খ্রিস্টাব্দে গুজরাট বিজয়ের পর টোডরমল গুজরাটের সমস্ত জমি জরিপ করে ভূমির গুণ ও আয়তন অনুসারে রাজস্ব স্থির করেন। 1575 খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ-বিহার ছাড়াও সাম্রাজ্যের সকল জমি খলিসা বা খাস জমিতে পরিণত করা হয়। এরপর 1582 খ্রিস্টাব্দে টোডরমল দেওয়ানী আশরাফৎ অথবা প্রধান রাজস্ব সচিব এ নিযুক্ত হন । টোডরমল গজ-ই-ইলাহি এক বিঘার আয়তন এক এককের 0.59 ভাগের সমান মাপের সমগ্র সাম্রাজ্যের জমিজরিপ যেমন এক বছরের জন্য রাজস্ব পরিমাণ ধার্য করা হয় এটি একসালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত আর পরবর্তীকালে আকবর 10 বছরের ফসলের নিরিক্ষে রাজস্ব নির্দেশ দিলে সেটি দশসালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত হয় । ফলে ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব এই ব্যবস্থাকে চরম দাওয়াই বলে অভিহিত করেছেন।1582 খ্রিস্টাব্দে টোডরমল রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করেন এবং তিন প্রকার রাজস্ব ব্যবস্থার প্রচলন করেন। তাঁর রাজস্ব নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রথমতঃ আবাদি জমি জরিপ দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকবিহার উৎপন্ন শষ্যর নিয়ন্ত্রণ তৃতীয়তঃ প্রত্যেক বিঘার রাজস্ব হার নির্ধারণ করা । এন.এ. সিদ্দিক জানিয়েছেন আকবরের সময় রাজস্ব নির্ধারণের প্রথা হিসেবে ছিল (ক) জাবতি প্রথা (খ) নাসাক (গ) গাল্লাবকস্ এবং কয়েকটি অতি প্রচলিত প্রথা ।
ক) জাবতি প্রথা : জাবতি কথার অর্থ হল জমি জরিপ এই ব্যবস্থা অনুসারে শস্যের পরিবতে নগদ টাকা রাজস্ব হিসেবে ধার্য করা হয় আর জমির উৎপাদিকা শক্তির উৎপাদন অনুসারে সকল চাষের জমি কে কোলাজ/ চাঁচর/ বানজার /তরোতি এই কয়টি ভাগে বিভক্ত করা হতো । কোলাজ-যে জমিতে সারাবছর চাষ হতো। চাঁচর-যে জমিকে তিন চার বছরের জন্য পতিত রাখা হতো। বানজার-যে জমি গুলিকে পাচঁ বছরের অধিকাংশ সময় পর্যন্ত পতিত রাখা হয়। তরোতি-যে জমি কিছুদিন চাষ করার পর পতিত রাখা হতো। উৎপাদন অনুসারে প্রথম তিন শ্রেণীর জমিকে উত্তম-মধ্যম অধম এই ভাবে ভাগ করে উৎপাদনের আনুমানিক গড়পড়তা হিসেবে শস্যের 1-3 অংশ হিসেবে রাজকর ধার্য করা হতো।এবং কৃষকদের নগদ মূল্যে রাজস্ব দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হতো কিছু তথ্য থেকে জানা যায় এই ব্যবস্থা গুজরাট বিহার মুলতান রাজপুতনার কিছু অংশে প্রবর্তিত হয়েছিল।
খ) নাসাক: এ ব্যবস্থায় জমিদারি প্রথা সমতুল্য ছিল। জমি জরিপ করে তার উৎপাদন শক্তি অনুসারে কর ধার্য করার পরিবর্তে একটি মোটামুটি অনুপাত এর উপর রাজস্ব স্থির করা হতো।এই ব্যবস্থা কেমন মাত্র বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল ইরফান হাবিব বলেছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাসাক রাজস্ব নির্ধারণের জন্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি বলে গণ্য করা হয়নি।
গ) গাল্লাবকস্: রাজস্ব নির্ধারণের তৃতীয় প্রথা ভাওয়ালী বা গাল্লাবকস্ নামে পরিচিত। ফরাসিতে এর নাম 'গল্লাবকসি্' এর অর্থ হলো ভাগ চাষ। রাজস্ব আদায়ের জন্য কোন মধ্যস্বত্বভোগী দের নিয়োগ করা হয়নি। আকবরের আমলে নগদ মুদ্রায় রাজস্ব আদায়ের প্রথাটি সুপরিচিত ছিল কারণ কোনো কারণে কৃষক যদি নগদে মুদ্রায় রাজস্বনা দিতে পারে তাহলে উৎপন্ন ফসলের বিনিময়ে তা গ্রহণ করার ব্যবস্থা ছিল। শাসন ব্যবস্থা ও রাজস্ব ব্যবস্থার সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সুবায় গড়ে তোলা হয়এবং সুবাকে পরে সরকারে ও পরগনায় বিভক্ত করা হয়। আবার কয়টি গ্রাম নিয়ে একটি পরগনা গঠিত হয়। প্রত্যেক সুবায় একজন করে দেওয়ান সরকারি আমিন এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্য বিটি কচি ও পাটোয়ারী , কানুনগো চৌধুরী প্রভূতি কর্মচারী নিযুক্ত করতেন ; যারা সংশ্লিষ্ট ছিল রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থায় আর অন্যদিকে কৃষকরা যাতে উৎপীড়িত না হয় সেদিকেও আকবর আমিনকে কড়া নজর দিতে বলেছেন।
পরবর্তীতে কৃষক কুলের ওপর আকবরের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রভাব ছিল বেশ উন্নত। রাজকর সুনির্দিষ্ট হওয়ায় অন্যায় ভাবে কর আদায়ের অবকাশ ছিল না। জমির উপর কৃষকদের অধিকার স্বীকৃত হয় এবং দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পায়। কৃষির উন্নতি ঘটে এবং সম্রাটের আয় অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।রাজস্ব সুনির্দিষ্ট হওয়ায় রাজকর্মচারীদের পক্ষে তা আত্মসাৎ করার উপায় ছিল না । দুর্ভিক্ষ বা ফসল ও অজন্মার সময় কর মাফ করার ব্যবস্থা ছিল।এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ আকবরের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন- "সম্রাটের রাজস্ব নীতি বাস্তববাদী ও সুনিশ্চিত।" অন্যদিকে আকবরের রাজস্ব নীতি সম্পর্কে যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, কৃষক ও সরকারের সংগ্রামের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হতো।তহশিলদার ও কৃষকদের মধ্যে সংগ্রাম লেগেই থাকত। ডক্টর এ.এল. শ্রীবাস্তব আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে-সৃষ্টি করে জননিরাপত্তা দিতে সক্ষম হয়েছিল।এবং রাজস্ব বিভাগ ও তৎকালীন মধ্যযুগের বিশ্ব ইতিহাসে অত্যন্ত একটি সন্তোষজনক বিভাগের পরিণত হয়েছিল তাই বলা যায়-"Akbar is entitled to rank among the greatest revenue administrator of the medieval world"❋ 2. মুঘলসাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি আলােচনা কর?
ロ পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসেবে জোর দিয়েছেন ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি এবং ধর্মনীতির উপর। আধুনিক গবেষকগণ জোর দিচ্ছেন রাজনীতি, অর্থনীতি এবং বৈদেশিক নীতির উপর। এর সঙ্গে সম্রাটের ব্যক্তিগত যােগ্যতাও যুক্ত করা প্রয়ােজন। তবে দাক্ষিণাত্য নীতি যে, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল, সেকথা সকল দেশের সর্বকালীন ঐতি-হাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পশ্চাতে যে কারণ ছিল তা এভাবে আলােচনা করা যেতে পারে –
⦿ দাক্ষিণাত্য নীতি ; বিজাপুর এবং গােলকুণ্ডা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে ঔরঙ্গজেব আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেলেন এইজন্য যে, সিয়া সুন্নী রাজ্য দুটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং দাক্ষিণাত্য নীতির উদ্দেশ্য সফল কাম হতে চলেছে। এদিকে মারাঠাগণ উত্তর ভারতের রাজপুতদের মত ক্রমে ক্রমে প্রবল শত্রুতে পরিণত হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা এবং হিন্দু বিদ্বেষ মারাঠাদের উগ্র জাতীয়তাবােধ জাগ্রত করে তুলেছিল। শিবাজী মারাঠা জাতিকে যেভাবে স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাতে মারাঠাগণ মুঘল সাম্রাজ্যের বন্ধনকে ছিন্ন করবার স্বপ্ন দেখতে পেয়েছিল। ঔরঙ্গজেব সর্বশক্তি প্রয়ােগ করে মারাঠাদের দুর্গগুলি দখল করতে উদ্যোগী হন। এরপর ১৭০০-১৭০৫ খ্রিঃ মধ্যে ঔরঙ্গজেব সমগ্র দাক্ষিণাত্যে সামরিক তৎপরতা বজায় রাখতে ব্যপৃত থাকেন। বন্যা, মহামারী, মারাঠাশক্তির ক্রমাগত আক্রমন মুঘল সৈনদের বিভ্রান্ত করে তােলে এবং মুঘল সেনাধক্ষ ও অভিজাতদের মধ্যে হতাশা সংশয়, বিক্ষোভ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়।
তাছাড়া মুঘল দুর্গের এই অস্তাচলগামী অবস্থায় জায়গীরদারগণ মারাঠাদের সঙ্গে গােপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে আপনাদের নিরাপত্তার জন্য মারাঠাদের চৌথ দিতে রাজী হয়। পরিশেষে ঔরঙ্গজেব মারাঠাদের সঙ্গে আলাপ আলােচনা করতে বাধ্য হন এবং মুঘল হস্তে বন্দী শম্ভুজীর পুত্র শাহ্ ও তার মাতাকে মুক্তি দিতে সম্মত হন। তাছাড়া শাহুকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করতে এবং তাকে সাত হাজারী মনসব দিতে রাজী হন।
কিন্তু মারাঠাদের যথার্থ মনােভাব না পেয়ে সন্দিগ্ধ ঔরঙ্গজেব শেষ পর্যন্ত শাহুকে মুক্তি দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এর পরেই ১৭০৭ খ্রিঃ এই দ্বন্দ্ব-মুখর বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে তার মৃত্যু ঘটে। তার-এই করুণ মৃত্যু মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে। এই মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত অতিদ্রুত ভেঙে পড়ে। তবে মৃত্যুর পূর্বে শাহুকে তিনি যে দন্ড-বিধান দিয়েছিলেন, তার ফলস্বরূপ শাহুকে ১৭০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত বন্দি থাকতে হয়েছিল। এরপর ১৭০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজারাম মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন। তার মৃত্যুর পরও তারাবাঈ মারাঠা জাতীর সম্মান রক্ষার্থে আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে যান । ঔরঙ্গজেব বহু প্রচেষ্টা স্বত্ত্বেও মারাঠা শক্তিকে বিদ্ধস্ত করতে পারেন নি। তাই তাদের দাক্ষিণাত্যে নীতির ব্যর্থতা ছিল অনিবার্য।
প্রশাসনিক ব্যর্থতা ; ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্য বিশাল বিস্তৃতি পেয়েছিল।সেই সঙ্গে প্রশাসনিক কাজের চাপ বৃদ্ধি পায়। সম্রাটের জনকল্যাণনীতি সাম্রাজ্যের দূরপ্রান্তে কর্মচারীদের দ্বারা অত্যাচার নীতিতে পর্যবসিত হলেও কেউ জানতে পারত না। সম্রাট যে সমস্ত কর লােপ করেছিলেন, বার বার তার জন্য আদেশ জারি করা থেকে মনে হয় দূরবর্তী এলাকার মুঘল কর্মচারীরা ওই আদেশের কোনাে মূল্য দিত না।
⦿ সম্রাটের ব্যক্তিগত যােগ্যতা ; ঔরঙ্গজেব ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাটদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর ব্যক্তিগত যােগ্যতা ও দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। ব্যক্তি-নির্ভর সামরিক আনুগত্য নির্ভর করত সামরিক সাফল্যের উপর। মুঘল সেনাবাহিনী ছিল বিভিন্ন জাতি,ধর্মের সৈনিক নিয়ে সম্রাটের গঠিত। বেশির ভাগই ছিল বিদেশি। এই দেশের অখন্ডতা ও স্বাধীনতার জন্য তাদের কোনাে মাথাব্যথা ছিল না। সৈনিকদের আনুগত্য ছিল সেনাপতির উপর। সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধে যােগ দিয়ে ব্যক্তিগত দক্ষতায় যতক্ষণ সেনা-বাহিনীকে জয় এনে দিতে পারবে, ততক্ষণ সম্রাটের প্রতি সেনাবাহিনীর সম্রম অক্ষুন্ন থাকবে।কিন্তু সামরিক বিপর্যয় ঘটলেই সমস্ত ব্যবস্থা ওলট-পালট হয়ে যাবে। ঔরঙ্গজেব-পরবর্তী যুগে দক্ষ সম্রাটের অভাবে সেনাবাহিনীর আনুগত্য সম্রাটের প্রতি ছিল না। সুতরাং সম্রাট সেনাবাহিনীর উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন।
⦿ বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা ; বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কান্দাহার ও হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া। মুঘল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের পক্ষে এটা ছিল দুর্যোগের অশনি সংকেত। মুঘল সাম্রাজ্যের তিনদিকউপকূলবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও মুঘল সম্রাটদের কোনাে উপকূলীয় নীতি ছিল না। উপকূল সীমান্ত রক্ষার জন্য এবং ভারতের সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যের নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তােলা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু মুঘল সম্রাটই এদিকে দৃষ্টি দেননি। নাদির শাহ ও আহম্মদশাহ আবদালি মুঘল সাম্রাজ্য পুরােপুরি ধ্বংস করতে পারেননি। যা পেরেছিল উপকূল দিয়ে আগত ইংরেজ বণিকরা।
⦿ অর্থনৈতিক সংকট ; জমিদার, মানসবদার এবং সম্রাটদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছিল। একই সঙ্গে টাকার মূল্য কমে গিয়েছিল। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক এবং সামরিক খরচ বেড়ে গিয়েছিল। রাজস্ব আদায়ের প্রধান ক্ষেত্র কৃষিক্ষেত্রে সার্বিক উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল! তা সত্ত্বেও মুঘল প্রশাসন কৃষকদের উপর চাপ বাড়িয়ে চলেছিল। একই সঙ্গে ইউরােপীয় ব্যবসায়ীদের ছাড় দিয়েছিল অথচ সেখান থেকেই মােটা রাজস্ব আদায় সম্ভব ছিল। কৃষকদের উপর চাপ বাড়ানাের জন্য কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। ইরফান হাবিবের মতে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ ছিল কৃষক বিদ্রোহ।
⦿ অভিজাতদের দ্বন্দু ; শাসকশ্রেণি অর্থাৎ অভিজাত মনসবদার শ্রেণির মধ্যে ভালাে মনসব পাওয়ার জন্য গােষ্ঠী দ্বন্দ্ব ছিল। শক্তিশালী সম্রাটের অধীনে এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসত না। কিন্তু তবুও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষদিকে ভালাে মনসবের জন্য ক্রমশ গােষ্ঠীদ্বন্দ্ব বাড়ছিল। অথচ মনসবদাররাই ছিল সাম্রাজ্যের ভিত। দরবারে ইরানী, তুরানী ও হিন্দুস্থানী গােষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল। অভিজাতদের বিভিন্ন গােষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এইসব পরিস্থিতি যখন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিপন্ন করেছিল তখন ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট নাদির শাহের আক্রমণ মােগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।
❋ 3. মধ্যযুগের ভারতবর্ষের বা মুঘল যুগের ইতিহাসের প্রধান উপাদানগুলি সম্বন্ধে আলােচনা কর?
ロ সৃষ্টির প্রত্যুষ লগ্ন থেকে অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি মানব জীবনের যে প্রবহমান যাত্রা এগিয়ে চলেছে, ইতিহাস তার ধারাকে বহন করে চলেছে। একথা সথ্য যে বাস্তব জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যেই রয়েছে কোন না কোন উপাদানগত বৈশিষ্ট্য। ইতিহাস এই রীতির বহির্ভূত নয় তাই ঐতিহাসিকগণ যে যুগে বসেই ইতিহাস রচনা করুক না কেন, তাঁকে সেই যুগের সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ভৌগলিক অবস্থান, সাহিত্য, শিল্প এসব কিছু উপাদান নিতে হবেই হবে। কেননা ইতিহাস বস্তু নিরপেক্ষ নয়, ইতিহাসের দর্পণেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে অনেকটাই জাতির ভবিষ্যত।
একথা ঠিক যে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হজরত মহম্মদের সময়কাল থেকেই মুসলমানগণ ইতিহাস রচনা শুরু করেন। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে হজরত মহম্মদ
খলিফা, সুলতান ও সৌভ্রাতৃত্বের জীবনী লেখার সুত্রপাত ঘটে। ইতিহাস রচনার উষাকালে মুসলমানগণ আরবী ভাষাকেই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। এরপর পারসিক জাতীয়তাবাদের ফলে পারসিক ভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। ফলশ্রুতি হিসাবে এই ভাষা মুসলমানদের কাছে আদরণীয় হয়ে ওঠে এবং ঐতিহাসিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।
মধ্যযুগের ইতিহাস রচনায় উপাদান ছিল সুপ্রচুর। প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনায় শিলালিপি, কিংবদন্তী, মুদ্রা ও সাহিত্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপাদানগুলি সংগ্রহ করতে বিশেষ শ্রম করতে হত, কিন্তু মধ্যযুগের ঐতিহাসিক রচনায় এই সমস্ত ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করা বিশেষ শ্রম সাধ্য ছিল না। মধ্যযুগের ভারত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
একথা ঠিক যে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হজরত মহম্মদের সময়কাল থেকেই মুসলমানগণ ইতিহাস রচনা শুরু করেন। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে হজরত মহম্মদ
খলিফা, সুলতান ও সৌভ্রাতৃত্বের জীবনী লেখার সুত্রপাত ঘটে। ইতিহাস রচনার উষাকালে মুসলমানগণ আরবী ভাষাকেই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। এরপর পারসিক জাতীয়তাবাদের ফলে পারসিক ভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। ফলশ্রুতি হিসাবে এই ভাষা মুসলমানদের কাছে আদরণীয় হয়ে ওঠে এবং ঐতিহাসিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।
মধ্যযুগের ইতিহাস রচনায় উপাদান ছিল সুপ্রচুর। প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনায় শিলালিপি, কিংবদন্তী, মুদ্রা ও সাহিত্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপাদানগুলি সংগ্রহ করতে বিশেষ শ্রম করতে হত, কিন্তু মধ্যযুগের ঐতিহাসিক রচনায় এই সমস্ত ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করা বিশেষ শ্রম সাধ্য ছিল না। মধ্যযুগের ভারত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
⦿ চাচনামা :- আরবী ভাষায় রচিত চাচনামা থেকে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ইতিহাস সংগৃহীত হয়েছে। আবুবক্কর কুফী ফার্সি ভাষায় এর অনুবাদ করেছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে মহম্মদ-বিন - কাশীমের সিন্ধু অভিযানের পূর্বে এবং পরে সিন্ধু দেশের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।
⦿ তারিক-ই-সিন্ধ :- এই গ্রন্থটি ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। মীর মহম্মদ মাসুম এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। আরবদের সিন্ধু অভিযান থেকে শুরু করে মহামতি আকবরের সময়কাল পর্যন্ত বহু উল্লেখযােগ্য ঘটনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই গ্রন্থটিকে সমকালীন ইতিহাস না বলা গেলেও এর অভ্যন্তরে আরবদের সিন্ধু অভিযান এবং মহম্মদ বীন কাশিমের সাফল্য উদঘাটিত হয়েছে।
⦿ কিতাব-উল-ইয়ামিনি :- আবুনাসের বিন উৎবি 'কিতাব-উল-ইয়ামিনি' গ্রন্থের রচয়িতা। সবুক্তগীন (গজনীর সুলতান) ও সুলতান মামুদের রাজত্বকাল থেকে ১০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক ধারাবাহিক ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, গ্রন্থটি সাহিত্যরূপে বিবেচিত। একে - ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা সমীচীন হবে না। আবুনাসের তাঁর গ্রন্থে সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। যদিও এই গ্রন্থের মধ্যে তারিখ ও সময় সংক্রান্ত কিছু ভুলত্রুটি রয়েছে, তবুও এই
গ্রন্থটিতে সুলতান মামুদের প্রথম জীবন এবং তার কিছু কার্য সম্পাদনের উল্লেখযােগ্য বিবরণ পাওয়া যায়।
গ্রন্থটিতে সুলতান মামুদের প্রথম জীবন এবং তার কিছু কার্য সম্পাদনের উল্লেখযােগ্য বিবরণ পাওয়া যায়।
⦿ তারিখ-উল-হিন্দ :- অলবিরুণী 'তারিখ-উল-হিন্দ' গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থের মাধ্যমে সমসাময়িক যুগের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। অলবিরুরী সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন। আরবী ও ফার্সী ভাষায় তাঁর পান্ডিত্য রয়েছে। ভারতে স্বল্পকালীন অবস্থান করেই তিনি ধর্মসাহিত্য, হিন্দুদর্শন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানার্জন করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষার অতিও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট 'তারিখ-উল-হিন্দ' গ্রন্থ থেকে একাদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে ভারতের ধর্মবিজ্ঞান,সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক প্রয়ােজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের পূর্বকালীন অবস্থায় এক নিরাভরন চিত্র এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়।
⦿ মুঘল আমলে রচিত গ্রন্থাদি :- মুঘল আমলে ঐতিহাসিক গ্রন্থ ব্যাপক লিখিত হয়েছিল। এই যুগের ঐতিহাসিক রচনাগুলি বিশেষ উন্নত | সম্রাট এবং রাজ-রাজা দের ইতিহাস ব্যতীত এই যুগের ইতিহাসে স্থান পেয়েছিল সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক,সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থারমনােজ্ঞ চিত্র। এছাড়া মুঘল সম্রাট কেউ কেউ তাঁদের আত্মচরিত রচনা করে ইতিহাসের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।
আত্মচরিত ও ব্যক্তিগত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ব্যতীত মুঘল যুগের কিছু দরবারী ইতিহাস রচিত হয়েছে। পারস্যের প্রভাব প্রসূত হয়েই এই জাতীয় ইতিহাস রচিত হয়। সম্রাট আকবরের প্রচেষ্টায় - মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনা শুরু হয় এই রচনা ধারা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকে। তবে এই সরকারি গ্রন্থগুলি রচিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারি দলিল, প্রাদেশিক সরকারি দলিল কিংবা সরকারি নির্দেশের উপর ভিত্তি করে। তাই এই গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সম্রাটদের রাজত্বকালীন তথ্য পাওয়া যায়। আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবুল ফজল রচিত ‘আইন-ই- আকবরী’ ও ‘আকবর নামা’ নামক গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যায়। প্রথম গ্রন্থটিতে আকবরের রাজ্যশাসন-প্ৰণালী, আইনকানুন এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।
⦿ বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ :- মুঘল যুগের প্রাক্কালে যে সমস্ত বিদেশি পর্যটকগণ ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ইবনবতুতার নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁর রচিত ‘রাহলা’ সুলতানি আমলের একটি উল্লেখযােগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অভ্যন্তরে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে ভারতবাসীর আচার-আচরণ ও ভারতের সাধারণ অবস্থার বিচিত্র বিবরণ পাওয়া যায়। চৈনিক পর্যটক মা-হুয়ান ঞ্চদশ শতাব্দীতে দেশে এসেছিলেন এবং বঙ্গদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার জীবন্ত চিত্র লিপিবদ্ধ করেছিলেন। নিকালােকন্টি, আবদুর রজ্জাক, প্রমুখ পর্যটকগণ সুলতান আমলের বহুমূল্যবান তত্ত্ব রেখে গিয়েছেন। টেভারনিয়ার ,বার্নিয়ার, মানুচি প্রমুখ পর্যটকগন ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে এসেছিলেন এবং জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য উদঘাটন করে গিয়েছেন।
মুঘল যুগে মারাঠাগন ও ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তাদের একটি উল্লেখযােগ্য গ্রন্থের নাম - ‘সভাসদ-বাখর'। শিবাজীর সমসাময়িক কোন এক ঐতিহাসিক এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। রাজপুতগণওতাদের স্বজাতীয় ঐতিহাসিক তথ্য রেখে গিয়েছেন। রাজপুতচারণদের লিখিত 'চারণগীতি’ একটি নির্ভরযােগ্য ঐতিহাসিক দলিল। এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই ঐতিহাসিক টড তাঁর ‘রাজস্থানের ইতিহাস’ নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তবে একথা স্বীকার্য যে, টড সৃষ্ট এই গ্রন্থটি নির্ভরযােগ্য নয়। গ্রন্থ সাহেব’ ধর্মগ্রন্থ হলেও শিখদের ইতিহাস রচনার সহায়ক হিসাবে বিবেচিত।
মুঘল মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদানগুলির মধ্যে সমকালীন ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত তৎকালীন জীবনযাত্রার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস জানতে হলে অবশ্যই সাহিত্যের উপর নির্ভর হতে হবে। আমীর খসরু বিরচিত ‘খাজা- ইন-উল-ফুতুহ’ এবং মহম্মদ জায়েসী রচিত ‘পদ্মাভত’ বা ‘পদুমাবৎ' নামক গ্রন্থদ্বয় থেকে তদানীন্তন সমাজ এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের নির্ভরযােগ্য তথ্য পাওয়া যায়।
❋ 4. আকবরের রাজপুতনীতিটি পর্যালােচনা কর বা এই নীতির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল?
ロ ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহের পরাজয় ঘটলেও উত্তর ভারতের রাজপুত শক্তি সম্পূর্ণভাবে পর্যদস্ত হয় নি। যেমন তালিকোটার যুদ্ধে ১৫৬৫ পরাস্ত হলেও দক্ষিণ ভারতে হিন্দু শক্তির বিলােপ ঘটে নি। দুই শতাব্দীর পূর্বে হিন্দু শক্তির যে পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল, তা অব্যাহত থাকে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে তা নতুন করে প্রকাশ পায়। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে পরাজয়ের পরও শাসক জাতি ও সামরিক শক্তি হিসেবে উত্তর ভারতে রাজপুতদের প্রতিপত্তি অব্যাহত থাকে। শেরশাহ রাজপুত রাজন্যদের অনেক কে শক্তির পরিবর্তে প্রতারনার মাধ্যমে পরাস্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আকবরের রাজত্বকালে রাজপুতরা নতুন করে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু সাময়িকভাবে সমকালীন রাজনীতিতে ধর্মান্ধতার পরিবর্তে উদারতার প্রসার ঘটায় সেইরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি।
আকবরই সর্বপ্রথম বিচক্ষণতা ও উদারতার সঙ্গে রাজপুতদের ন্যায় এক সংগ্রামশীল জাতিকে মুঘল রাজবংশের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ করে তাদের বিরােধীতার অবসান ঘটাবার নীতি গ্রহণ করেন। এই দিক দিয়ে আকবরের রাজপুত নীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হলে রাজপুতদের সমর্থন ও সহযােগিতা একান্ত প্রয়ােজন। সামরিক শৌর্য ও প্রতিভার দিক দিয়ে তদানীন্তন ভারতে রাজপুতরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাদের বিরােধীতা মুঘল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিক দিয়ে ছিল বিপজ্জনক। সম্রাটের অনুচর বর্গের অধিকাংশই ছিল ভাগ্যান্বেষী ও লােভী। বাংলাদেশে মুঘল সেনা ও সমর অধিনায়করা বারংবার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল। সুতরাং এরূপ অবস্থায় রাজপুতদের সঙ্গে সহযােগীতার গুরুত্ব আকবর উপলব্ধি করেন। রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের মূলে আকবরের উদ্দেশ্য ছিল পুরাতন আভিজাত্য সম্প্রদায়ের ক্ষমতার সংকোচন। কারণ পুরাতন অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর আকবরের আস্থা ছিল না। এই রূপ বলা হয়ে থাকে, যে সকল রাজবংশ ভারত শাসন করেছিল তাদের মধ্যে তৈমুর বংশের ভিত্তি ছিল দুর্বল। সাম্রাজ্যের বিস্তার ও নিরাপত্তার জন্যই হিন্দু তথা রাজপুতদের সহানুভূতি অর্জন করতে তিনি যত্নবান হয়ে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করেন --
আকবরই সর্বপ্রথম বিচক্ষণতা ও উদারতার সঙ্গে রাজপুতদের ন্যায় এক সংগ্রামশীল জাতিকে মুঘল রাজবংশের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ করে তাদের বিরােধীতার অবসান ঘটাবার নীতি গ্রহণ করেন। এই দিক দিয়ে আকবরের রাজপুত নীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হলে রাজপুতদের সমর্থন ও সহযােগিতা একান্ত প্রয়ােজন। সামরিক শৌর্য ও প্রতিভার দিক দিয়ে তদানীন্তন ভারতে রাজপুতরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাদের বিরােধীতা মুঘল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিক দিয়ে ছিল বিপজ্জনক। সম্রাটের অনুচর বর্গের অধিকাংশই ছিল ভাগ্যান্বেষী ও লােভী। বাংলাদেশে মুঘল সেনা ও সমর অধিনায়করা বারংবার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল। সুতরাং এরূপ অবস্থায় রাজপুতদের সঙ্গে সহযােগীতার গুরুত্ব আকবর উপলব্ধি করেন। রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের মূলে আকবরের উদ্দেশ্য ছিল পুরাতন আভিজাত্য সম্প্রদায়ের ক্ষমতার সংকোচন। কারণ পুরাতন অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর আকবরের আস্থা ছিল না। এই রূপ বলা হয়ে থাকে, যে সকল রাজবংশ ভারত শাসন করেছিল তাদের মধ্যে তৈমুর বংশের ভিত্তি ছিল দুর্বল। সাম্রাজ্যের বিস্তার ও নিরাপত্তার জন্যই হিন্দু তথা রাজপুতদের সহানুভূতি অর্জন করতে তিনি যত্নবান হয়ে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করেন --
(ক) বৈবাহিক মিত্রতা স্থাপন – তিনি বিভিন্ন রাজপুত রাজবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিকানীর রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। ১৫৮৪ খ্রিঃ তিনি জয়পুরের ভগবানদাসের কন্যার সঙ্গে নিজ পুত্র সেলিমের বিবাহ দেন। আকবরের এই বৈবাহিক নীতির প্রসঙ্গে ড. বেণীপ্রসাদ বলেন, “It symbolised the down of a new era in Indian politics” এর ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি অধিকাংশ রাজপুত নৃপতি- বর্গের শুধু যে বিরােধীতারই অবসান হয়েছিল এমন নয়, তাদের সাহায্যে প্রায় সমগ্র ভারতে মুঘলের সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।
(খ) রাজপুতদের উচ্চপদে নিয়ােগ – সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের উচ্চপত্র রাজপুতদের নিয়ােগ করে তিনি তাদের আনুগত্য লাভ করেন। তাদের মধ্যে রাজা টোডরম,রাজা ভগবান দাস, রাজা মানসিংহ প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযােগ্য। আকবর উদার রাষ্ট্রীয় ও নীতি গ্রহণ করে এবং হিন্দুদের উপর থেকে জিজিয়া কর তুলে নিয়ে হিন্দু তথা রাজপুতদের শ্রদ্ধাভাজন হন।
⦿ রাজপুত নীতির ফলাফল - হিন্দুদের সন্তোষ বিধানের জন্য আকবর রাজপুতদের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে মেলামেশা করতেন। এছাড়া তিনি হিন্দু সমাজে বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করেন । এর ফলে সম্রাটের প্রতি হিন্দুদের আস্থা স্থাপিত হয়। হিন্দু তথা রাজপুতদের প্রতি সম্রাটের বুন্ধত্ব মূলক মনােভাব ও সদয় আচরণ ভারতে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। একথা অনস্বীকার্য যে, পূর্ববর্তী তুর্কীদের ন্যায় আকবর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও গৌরবের জন্য স্থানীয় স্বাধীন রাজ্যগুলি একের পর এক ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু পূর্বসূরীদের সঙ্গে আকবরের নীতির পার্থক্য হল এই যে, তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে স্থানীয় রাজন্য বর্গ অনেক কে তৈমুর বংশের অনুগত মিত্রে পরিণত করেছিলেন। উদার নীতির দ্বারা পরিচালি, হয়ে তিনি রাজপুতদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযােগিতা লাভ করেন। এখানেই তার নীতির বিরাট সাফল্য। বন্ধুত্ব মূলক নীতি গ্রহণ করেই আকবর রাজপুতদের বিরােধীতার অবসান ঘটিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সমর্থ হন। রাজ্য বিস্তারে ও রাজ্য শাসন ব্যাপারে মুঘল সম্রাটরা রাজপুতদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযােগিতা লাভ করেন। আকবরের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের মূলে ছিল রাজপুতদের সক্রিয় সহযােগিতা, সম্রাটের শত্রুদের বিরুদ্ধে রাজপুতরাই ছিলেন প্রধান অবলম্বন। রাজপুত রাজ্য গুলির মধ্যে একমাত্র মেবারই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকৃত হয়েছিল । কিন্তু অন্যান্য নৃপতিদের সাহায্যেই মুঘল সম্রাট মেবারের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করতে সমর্থ হন।
আকবরের রাজপুত নীতি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান কর্তৃক অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজেব কর্তৃক এই নীতি পরিত্যক্ত হলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হয় । রাজপুতদের সাহায্যে আকবর শুধু যে রাজ্যবিস্তার ও বিদ্রোহ দমন করেছিলেন তা নয়, তাদের সাহায্যে তিনি সাম্রাজ্য শাসন ব্যবস্থা সুষ্ট ও শক্তিশালী করতে সমর্থ হয়েছিলেন । আকবরের আমলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও হিন্দু তথা রাজপুতদের অবদান অস্বীকার করা যায় না।
আকবরের রাজপুত নীতি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান কর্তৃক অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজেব কর্তৃক এই নীতি পরিত্যক্ত হলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হয় । রাজপুতদের সাহায্যে আকবর শুধু যে রাজ্যবিস্তার ও বিদ্রোহ দমন করেছিলেন তা নয়, তাদের সাহায্যে তিনি সাম্রাজ্য শাসন ব্যবস্থা সুষ্ট ও শক্তিশালী করতে সমর্থ হয়েছিলেন । আকবরের আমলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও হিন্দু তথা রাজপুতদের অবদান অস্বীকার করা যায় না।
মূল্যায়ন - মুঘলদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন রাজপুতদেরও যােগ্যতা প্রমাণ করার ও পদোন্নতির সুযােগ এনে দিয়েছিল। অন্যত্র এই সুযােগ পাওয়ার সম্ভাবনা তাদের ছিলনা রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রী মুঘলদের রাজনীতির এক ভিত্তি প্রস্তর হিসেবে গণ্য করা যায়। রাজপুতানায় শাসক সম্প্রদায়ের মর্যাদা লাভ করা ছাড়াও বহু রাজপুত জমিদার উত্তর ভারতে ছড়িয়েছিল। এই অবস্থায় বিশিষ্ট রাজাদের সঙ্গে বােঝাপড়া অপেক্ষা রাজপুতদের সঙ্গে এক সার্বিক মৈত্রী স্থাপনের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। সতীশচন্দ্র বলেছেন “ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত একটি মিশ্র শাসকগােষ্ঠী সংগঠনের লক্ষ্য বস্তুর দিকে এই রাজপুত মৈত্রী একটি সুদূর প্রসারী ও অর্থবহ পদক্ষেপ।”
❋ 5. মুঘল সম্রাটের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত লেখো?
ロ মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে কান্দাহার নামক অঞ্চলটি মুঘল-সাম্রাজ্যের হস্তচ্যুত হয়েছিল এবং ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত তা পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টাই করা হয় নি। এই বৎসর শাহজাহান কান্দাহার পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে প্রয়াসী হন। সেই সময় পারস্য সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আলিমদান খাঁ কান্দাহার শাসন করছিলেন। শাহজাহানের কান্দাহার পুনরুদ্ধারের সংকল্পের সংবাদ পেয়ে আলিমর্দান খাঁ পারস্যের শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু পারস্যের শাহ আলিমর্দানকে সন্দেহ করে তাকে
কোন সাহায্যদান করা থেকে বিরত থাকেন এবং আলিমদানকে বন্দি করার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। ফলে পারস্যের শাহের সঙ্গে আলিমদানের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠে।এই সুযােগে শাহজাহান আলিমদানকে
উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করে কান্দাহার দখল করেন এবং আলিমদানকে দিল্লীতে আশ্রয় দেন। শাহজাহান আলিমর্দানকে নানা সম্মানে ভূষিত করে কাশ্মীর ও কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।
কোন সাহায্যদান করা থেকে বিরত থাকেন এবং আলিমদানকে বন্দি করার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। ফলে পারস্যের শাহের সঙ্গে আলিমদানের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠে।এই সুযােগে শাহজাহান আলিমদানকে
উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করে কান্দাহার দখল করেন এবং আলিমদানকে দিল্লীতে আশ্রয় দেন। শাহজাহান আলিমর্দানকে নানা সম্মানে ভূষিত করে কাশ্মীর ও কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।
⦿ কান্দাহারের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযানের ব্যর্থতা :- কান্দাহার দখল করার ব্যাপারে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে শাহজাহান প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লা ও ঔরঙ্গজেবকে এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ কান্দাহারে প্রেরণ করেন কিন্তু এই অভিযানও ব্যর্থ হয়। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের নেতৃত্বে কান্দাহারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান প্রেরিত হয়। দুই মাস মুঘল বাহিনী কান্দাহার অবরুদ্ধ অবস্থায় রেখেও শেষ পর্যন্ত তা দখল করতে ব্যর্থ হয়। পারসিক গােলন্দাজবাহিনীর দক্ষতা মুঘলদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে। ঔরঙ্গজেব আরও কিছুদিন কান্দাহার অবরােধ করে রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু শাহজাহানের আদেশে মােগল-বাহিনী কান্দাহার পরিত্যাগ করে। কান্দাহার পুনরুদ্ধারের কাজ সম্পন্ন করার জন্য ঔরঙ্গজেব আরও বেশী কিছু সময় প্রার্থনা করলে, শাহজাহান তাকে এইভাবে উত্তর দেন, “যদি আমি বিশ্বাস করিতাম যে তুমি (ঔরঙ্গজেব) কান্দাহার দখলে সমর্থ, তাহা হইলে তােমায় আরও কিছু সময় দিতাম । প্রতিটি মানুষ কিছু কিছু কাজ করিতে সক্ষম । জ্ঞানীরা বলেন যে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোন পরামর্শের প্রতীক্ষা করে না।”
কান্দাহারের পুনরুদ্ধারের তৃতীয় অভিযানের অধিনায়ক হিসাবে যুবরাজ দারা প্রেরিত হন। অভিযানের প্রাক্কালে দারা দম্ভ করে বলেছিলেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি কার্য উদ্ধার করবেন। ব্যাপকভাবে এই অভিযানের প্রস্তুতি করা হয় এবং প্রচুর অর্থ নিয়ােজিত করা হয়। কয়েক মাস ধরে কান্দাহার অবরুদ্ধ অবস্থায় রেখে শেষ পর্যন্ত মুঘলবাহিনী প্রত্যাবর্তন করে এরপর কান্দাহার পুনরুদ্ধারের আর কোন চেষ্টা করা হয় নি।
কান্দাহারের পুনরুদ্ধারের তৃতীয় অভিযানের অধিনায়ক হিসাবে যুবরাজ দারা প্রেরিত হন। অভিযানের প্রাক্কালে দারা দম্ভ করে বলেছিলেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি কার্য উদ্ধার করবেন। ব্যাপকভাবে এই অভিযানের প্রস্তুতি করা হয় এবং প্রচুর অর্থ নিয়ােজিত করা হয়। কয়েক মাস ধরে কান্দাহার অবরুদ্ধ অবস্থায় রেখে শেষ পর্যন্ত মুঘলবাহিনী প্রত্যাবর্তন করে এরপর কান্দাহার পুনরুদ্ধারের আর কোন চেষ্টা করা হয় নি।
⦿ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-নীতির ফলাফল :-
- উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বহু যুদ্ধবিগ্রহের ফলে মুঘল রাজকোষের প্রভূত ক্ষতিহয় পরপর তিনবার কান্দাহার অবরােধের ফলে প্রায় বারাে কোটি টাকা ব্যয় হয়।
- যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে বহু সুদক্ষ সেনা ও সেনাপতির প্রাণনাশ হয়।
- ক্রমাগত ব্যর্থতার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের মর্যাদা বিনষ্ট হয় এবং মুঘল সামরিক বিভাগের দক্ষতা বহুলাংশে ক্ষুন্ন হয়।
- মুঘল সেনাবাহিনীর দুর্বলতা প্রকাশ পেলে দাক্ষিণাত্যে মারাঠারা দুধর্ষহয়ে উঠবার সুযােগ পায়।
- মুঘল অভিযানের ব্যর্থতার ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পারস্য সাম্রাজ্যের আধিপত্যপুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা মুঘল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিক দিয়ে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এই কারণে এরূপ বলা হয়ে থাকে, “For yours after words the Persian Peril hung like a dark cloud on the western frontier of India.”